যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপ্রাচ্য নীতির বিষয়ে বিশেষ একটি দিক রয়েছে। ১৯ শতকের গোড়ার দিকে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির মূল উৎস ‘ত্রিপলিটান যুদ্ধ’। যা ১৭৭৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার পরপরই সংঘটিত হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তা আরও বিস্তৃত হয়ে ওঠে।
স্নায়ুযুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়নকে এই অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার থেকে বিরত রাখার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্রনীতিতে কমিউনিস্ট-বিরোধী এবং সোভিয়েত-বিরোধী শাসনব্যবস্থাগুলোকে বিভিন্ন রূপে ব্যাপক সমর্থন দেওয়ার বিষয়টি দেখা যায়। এ লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ অগ্রাধিকারের মধ্যে ছিল আরব-ইসরাইল সংঘাতের শীর্ষে সোভিয়েত-সমর্থিত প্রতিবেশী আরব দেশগুলোর বিরুদ্ধে ইহুদি ইসরাইল রাষ্ট্রটির প্রতি সমর্থন।
সেই মধ্যপ্রাচ্য নীতির ভিত্তিতে পাকিস্তান ও ইসরাইলকে নীরবে একত্রিত করার চেষ্টা করছে যুক্তরাষ্ট্র। কৌশলগতভাবে ইসরাইলকে যাতে পাকিস্তান স্বীকৃতি দেয়, সেদিকে ঠেলে দিচ্ছে ওয়াশিংটন। এর স্পষ্ট ইঙ্গিতগুলো দেখা যায় ২০২৫ সালের নভেম্বরে, পাকিস্তানি কর্মকর্তাদের সঙ্গে ইসরাইল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের একাধিক প্রকাশ্য ও নজরকাড়া সাক্ষাতে।
বিষয়টি একটি তথ্যবহুল লেখা লিখেছেন এশিয়া টাইমসের সাংবাদিক ইমরান খুরশিদ। তার নিবন্ধনটির বাংলা অনুবাদ পাঠকদের কাছে উপস্থাপন করা হলো—
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সাম্প্রতিক মাসগুলোতে পাকিস্তানের ইসরাইলের সঙ্গে প্রকাশ্য ও গোপন যোগাযোগ অভূতপূর্ব মাত্রায় বেড়েছে। ধারাবাহিক প্রকাশ্য সাক্ষাৎ, প্রতীকী রাজনৈতিক ইঙ্গিত এবং সমন্বিত আঞ্চলিক কূটনীতি ইঙ্গিত দিচ্ছে- ভূরাজনৈতিক বাস্তবতা বদলে যাচ্ছে।
এ ঘটনাগুলো যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপ্রাচ্য নীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিলে যায়। বিশেষ করে শান্তভাবে এগিয়ে নেওয়া আব্রাহাম অ্যাকর্ডস ২.০-এর প্রসারণ পরিকল্পনার সঙ্গে। যদিও জনপ্রিয় বিশ্লেষণগুলোতে প্রায়ই বলা হয়- মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পকে যুদ্ধবিরতির কৃতিত্ব ভারতের না দেওয়া বা রাশিয়া থেকে সস্তায় তেল কেনা- এসবের কারণে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের প্রতি উষ্ণ হয়েছে, কিন্তু এসব ব্যাখ্যা যথেষ্ট নয়।
এগুলো কেবল দ্বিপাক্ষিক বা অর্থনৈতিক দিককে গুরুত্ব দেয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের গভীরতর কৌশলগত ও প্রতীকী বিবেচনাগুলোকে উপেক্ষা করে। এর মধ্যে রয়েছে পাকিস্তানের পারমাণবিক অবস্থান, মুসলিম বিশ্বের জনমতের ওপর এর প্রভাব এবং গাজাপরবর্তী আঞ্চলিক পুনর্গঠন। একটি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দেখা যায়- এ প্রক্রিয়ায় তিনটি প্রধান পক্ষ রয়েছে। তারা হলো- পাকিস্তান, ইসরাইল এবং যুক্তরাষ্ট্র।
ইমরান খুরশিদ আরও লেখেন, ইসলামাবাদ যাতে ইসরাইলকে স্বীকৃতির দেয়, সেদিকে পাকিস্তানকে ঠেলে দিচ্ছে ওয়াশিংটন। একই সঙ্গে নিজের আঞ্চলিক ও অভ্যন্তরীণ স্বার্থও সামলাচ্ছে। এ নীতিগত পরিবর্তনের সবচেয়ে স্পষ্ট ইঙ্গিতগুলো দেখা যায় ২০২৫ সালের নভেম্বরে, পাকিস্তানি কর্মকর্তাদের সঙ্গে ইসরাইল সংযুক্ত ব্যক্তিদের একাধিক প্রকাশ্য ও নজরকাড়া সাক্ষাতে। গত ৪ নভেম্বর লন্ডনের ওয়ার্ল্ড ট্রাভেল মার্কেট ফেয়ারে ইসরাইলের পর্যটন বিভাগের মহাপরিচালক মাইকেল ইজহাকভ প্রকাশ্যে সাক্ষাৎ করেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সারদার ইয়াসির ইলিয়াস খানের সঙ্গে। দুদেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও এই প্রকাশ্য কুশল বিনিময় ছিল অত্যন্ত ব্যতিক্রমী। যা উভয় পক্ষের ‘অসম্ভব’ দৃশ্যকল্পকে স্বাভাবিক করার ইঙ্গিত দেয়।
দ্বিতীয় সংকেত পাওয়া যায় প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে জাতিসংঘ অধিবেশনে অংশ নিতে নিউইয়র্ক সফরের সময়। নিউইয়র্কের কূটনৈতিক মহলে খবর ছড়ায় যে, শরিফের সঙ্গে আমেরিকান জিউইশ কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট ড্যানিয়েল রোজেনের একটি নীরব সাক্ষাৎ হয়েছে।
ইসলামাবাদ কিংবা এজেসি কেউই এটি প্রকাশ্যে স্বীকার করেনি। পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংবেদনশীলতার কারণে তা প্রত্যাশিত। কিন্তু অস্বীকার না করায় ধারণা আরও দৃঢ় হয় যে উচ্চপর্যায়ের যোগাযোগ আড়ালে চলছে। এসব ঘটনাই মিলে একটি বৃহত্তর প্রবণতা তৈরি করে- পরোক্ষ যোগাযোগের বিস্তার এবং নীরব অনুসন্ধানী কূটনীতি।
১৩ অক্টোবর শারম আল-শেখ সম্মেলন এ নতুন ভূমিকাকে আরও জোরালো করে। গাজা যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকটি ‘মুসলিম ঐক্যের’ প্রদর্শন হিসেবে উপস্থাপিত হলেও সংঘাতে জড়িত মূল পক্ষ ইসরাইল ও হামাসকে বাদ দিয়ে এটি মূলত প্রতীকী ছিল, যা যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবকে সংহত করা এবং আঞ্চলিক সমন্বয় প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ডিজাইন করা হয়েছিল। এটি দেখায় কীভাবে ওয়াশিংটন পাকিস্তানসহ গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে যুক্তরাষ্ট্রবান্ধব বয়ানের পক্ষে সাজিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে, মানবিক সহায়তা সমন্বয়ে নেতৃত্ব দিয়েছে এবং নিজের আঞ্চলিক কাঠামোকে আরও মজবুত করেছে। সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয় এমন এক সময়ে, যখন পৃথিবীর নানা স্থানে ইসরাইলের বিরুদ্ধে চাপ ইতিহাসে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে।
তিনি আরও লেখেন, গাজায় ইসরাইলি কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে বিশ্বব্যাপী নজিরবিহীন জনমত গড়ে ওঠে; ফ্রান্স, স্পেন, আয়ারল্যান্ড, নরওয়ে ও বেলজিয়ামসহ ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশ আনুষ্ঠানিকভাবে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার দিকে এগিয়ে যায়। ইউরোপীয় সরকারগুলো নিষেধাজ্ঞা, অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা এবং বাণিজ্য সুবিধা স্থগিতের বিষয়গুলো আলোচনা করতে থাকে। মহাদেশজুড়ে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দেয়। অ্যাক্টিভিস্ট নৌযান, মানবিক মিশন ও আইনি চ্যালেঞ্জ ইসরাইলের নীতির বিরুদ্ধে কঠোর সুর তোলে- যা আগের কোনো সংঘাতে দেখা যায়নি এমন নাগরিক প্রতিরোধের নতুন ঢেউ তৈরি করে।







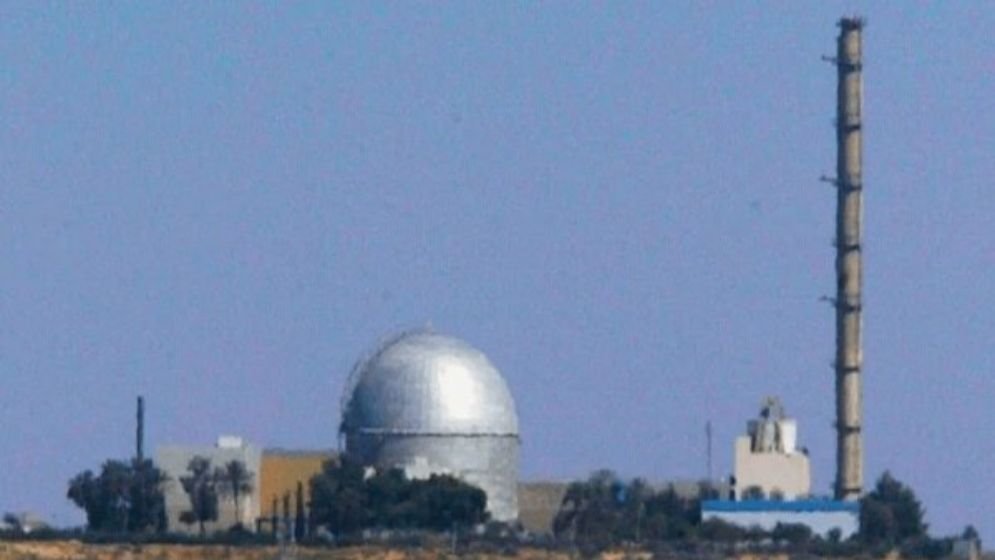

চলমান নিউইয়র্ক ফেসবুক পেজ লাইক দিন
আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করুন